
ড. মিহির কুমার রায়

৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল গগনচুম্বী। জনগণ আশা করেছিল নতুন অন্তর্বর্তী সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করবে, অর্থনীতিকে গতিশীল করবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাওয়া ছিল একটি গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করে মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দেও য়া এবং একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরে যাওয়া যদিও আগামী ফেব্রোয়ারীতে রমযানের আগে নিবর্চনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এক বছর পর যদিও কয়েকটা অর্থনৈতিক সূচক কিছুটা উন্নতি করেছে, অধিকাংশ সূচকই এখনো আগের দুর্বল অবস্থান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। কিছু ইতিবাচক উদ্যোগের ফলে অর্থনীতি উপকৃত হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ ছিল উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। এক বছরের ব্যবধানে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ১১ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ৮.৫৫ শতাংশে এবং খাদ্যমূল্যস্ফীতি ১৪ শতাংশ থেকে প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। তবে সাধারণ মানুষের অভিযোগ, আয়ের তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় এখনো আগের চেয়ে বেশি। এখন পর্য়ায়ক্রমে মূল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। যেমন :
১. সার্বিকভাবে বলা যায়, ব্যাংক খাতের কিছুটা উন্নতি হলেও দুর্দশা কাটেনি। তবে ব্যাংক খাত নিয়ে আগের মতো আতঙ্ক নেই । ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএফ) সাবেক নির্বাহী পরিচালক বলেন, ‘বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরকারের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয়েছে, যা ব্যাংকব্যবস্থাকে দুর্বল করে তুলেছে। এখন পরিবর্তনের আশা আছে এবং বর্তমান সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে সুশাসন ফেরানোটা জরুরি। ব্যাংক খাতে যত দ্রুত সুশাসন ফেরাতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি ব্যাংক খাত ঘুরে দাঁড়াবে।’ তিনি বলেন, ‘গত বছর গ্রাহকদের আস্থার সংকট ছিল। যেটা এখন অনেক কেটে গেছে। যদিও কিছু কিছু ব্যাংক এখনও আস্থা অর্জন করতে পারেনি। তবে কঠোর পদক্ষেপ যা নেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা গেলে ব্যাংক খাত আরও ভালো করবে।’
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি, আর আইএমএফের বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে তা ২৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান গত বুধবার রাতে এসব তথ্য জানান। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ বর্তমানে ২০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি, যা দিয়ে সাড়ে তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব।
৩. রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ স্থিতিশীল থাকায় ডলারের ওপর চাপ কমেছে। গত ১০ মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি না করায় পরিস্থিতি আরও উন্নত হয়েছে। এর পাশাপাশি বাজেট সহায়তা ও ঋণ হিসেবে কয়েক বিলিয়ন ডলার বিদেশি সহায়তাও রিজার্ভ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে আমদানি নিয়ন্ত্রিত থাকায় ডলারের চাহিদা কমে বিনিময় হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে ডলারের দাম অতিরিক্ত কমে যাওয়া রোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিলামের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ডলার কিনছে।
৪. অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর ব্যাংকগুলোয় তদারকি জোরদার করে বাংলাদেশ ব্যাংক। পাশাপাশি এতদিন নীতিমালায় যেসব ছাড় দেওয়া হয়েছিল, তা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে। এ ছাড়া আগের সরকারের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংকগুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাংক রেজুলেশন অধ্যাদেশ অনুমোদন দিয়েছে। যার অধীন ব্যাংক একীভূত, অধিগ্রহণ ও অবসায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। এজন্য সংকটে পড়া ব্যাংকগুলোর সম্পদের মান ও সুবিধাভোগী যাচাইয়ে বিদেশি নিরীক্ষক দিয়ে নিরীক্ষা চলছে। যার মাধ্যমে ৬টি ইসলামী ধারার ব্যাংককে একীভূত করার পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব ব্যাংককে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও দেশি ভালো বিনিয়োগকারী এনে শক্তিশালী করার চিন্তা চলছে।
৫. নতুন সরকার অর্থ পাচার রোধে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ায় সুফল পেয়েছে দেশের অর্থনীতি। এদিকে অর্থ পাচার রোধে সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এখন কিছুটা সক্রিয় হয়েছে। তবে ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছেন অর্থ আত্মসাতে জড়িত গ্রাহক ও ব্যাংক কর্মকর্তারা।
৬. মোট ১৪টি ব্যাংকের বোর্ড পুনর্গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। যা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে একীভূত করে একটি সুদৃঢ়, স্বচ্ছ ও সংগঠিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার অংশ। তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর জানিয়েছিলেন, দুর্বল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো একীভূত করা হবে, যাতে তাদের কার্যক্রম আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ হয়। সরকারের চলমান অর্থনৈতিক সংস্কারের অংশ হিসেবে ছয়টি নতুন আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যার মধ্যে ব্যাংক রেজুলেশন অ্যাক্ট ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ও ব্যাংক কোম্পানি অ্যাক্ট সংশোধনের কাজও চলছে।
৭. প্রবাসী বাংলাদেশিরা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেকর্ড পরিমাণ ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছে। যা দেশের ইতিহাসে এক অর্থবছরে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ। তার আগের অর্থবছর ২০২৩-২৪ রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার। যার তুলনায় রেমিট্যান্স প্রবাহ ২৬ দশমিক ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং রেমিট্যান্স আসায় গত অর্থবছরের মাস হিসেবে সর্বোচ্চ, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে। রেমিট্যান্সের সেই জোয়ার ২০২৫-২৬ অর্থবছরেও চলমান আছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দুই দশমিক ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। আগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় এটি প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি। এমনকি আগস্ট মাসের প্রথম পাঁচ দিনেও এই ধারা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, আগস্টের প্রথম পাঁচ দিনে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৮১ দশমিক ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। গত বছরের একই সময়ে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল ১৮১ মিলিয়ন ডলার।
৮. বিগত সরকারের আমলে অনিয়মের মাধ্যমে ভুয়া বা বেনামে ঋণ দেওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংক প্রয়োজনীয় ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (সিআরআর) রাখতে ব্যর্থ হলে ব্যাংকটিকে ২ হাজার ৩০৮ কোটি টাকা জরুরি ডিমান্ড লোন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মোট পরিশোধিত ঋণের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক জুনে ৮০৮ কোটি এবং ৩১ জুলাই আরও ৭০০ কোটি টাকা পরিশোধ করে। এর ফলে এখন প্রায় ৮০০ কোটি টাকার ঋণ বকেয়া রয়েছে। ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (সিআরআর) হলো একটি ব্যাংকের গ্রাহক আমানতের সেই অংশ, যা ঋণ হিসেবে বিতরণ না করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত ও শরিয়াহভিত্তিক উভয় ব্যাংককেই মোট আমানতের ৪ শতাংশ সিআরআর হিসেবে জমা রাখতে হয়।
৯. তবুও জ্বালানি সংকট ও আর্থিক খাতে জটিলতা রয়ে গেছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের কারণে বিভিন্ন প্রণোদনা বন্ধ হওয়া, উচ্চ সুদের হার এবং বিনিয়োগ হ্রাস আগামী অর্থবছরগুলোতেও প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলবে। অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ, টেকসই বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে এবং প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সরকারকে আরও মনোযোগী হতে হবে।
১০. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২৫ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ। ২০২৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৪ দশমিক ২২ শতাংশ। কম প্রবৃদ্ধির পেছনে রয়েছে বিনিয়োগের ঘাটতি, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সরবরাহ ব্যবস্থা-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, চাহিদার হ্রাস এবং সঠিক আর্থিক প্রণোদনার অভাবের মতো সমস্যা।
১১. উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সুদের হারে বিধিনিষেধ শিথিল করে বাজারভিত্তিক করা হয়েছে। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি এবং সরকারি প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছে। প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যে আমদানি শুল্ক কমিয়ে, দৈনন্দিন পণ্যের ক্ষেত্রে এলসি-বিষয়ক বাধ্যবাধকতা তুলে নিয়ে এবং খাদ্য ও সার আমদানিকারকদের জন্য ঋণের সুবিধা দিয়ে সরবরাহজনিত সমস্যা প্রশমনের চেষ্টা করা হয়েছে যাতে মূল্যস্ফীতি না বাড়ে। প্রথম দিকে তেমন ফলাফল দেখা না গেলেও মূল্যস্ফীতি এখন কমার দিকে। দীর্ঘ দুই বছরের বেশি সময় ধরে মূল্যস্ফীতি দুই অংকে থাকার পর তা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। জুলাই ২০২৪-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ, যা ২০২৫ সালের জুনে এসে ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমেছে।
১২. অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর সবচেয়ে আলোচিত দিক ছিল বিভিন্ন খাতে সংস্কার উদ্যোগ। যদিও সরাসরি অর্থনৈতিক খাতে সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়নি, পরিকল্পনা উপদেষ্টা একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল সমতা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল তৈরি করা। এই টাস্কফোর্স রিপোর্টে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্টটি প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করা হলেও সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো স্বল্পমেয়াদে কিছু সুপারিশের বাস্তবায়নে আগ্রহ দেখায়নি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালী করতে পরিকল্পনা উপদেষ্টা আরো একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছেন যাতে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উন্নত হয়। আশা করা যায়, এখান থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।
১৩. আলোচিত আরেকটি সংস্কার হলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ( এনবিআর) পুনর্গঠন। গত ১২ মে সরকার ‘রেভিনিউ পলিসি অ্যান্ড রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট অর্ডিন্যান্স’ জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে দুটি আলাদা বিভাগে ভাগ করার ঘোষণা দেয়—‘রেভিনিউ পলিসি বিভাগ’ এবং ‘রেভিনিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ’। এটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণ কর্মসূচির একটি শর্ত ছিল। তবে কর ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির জন্য বহুদিন ধরেই অর্থনীতিবিদ ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা এ ধরনের বিভাজনের সুপারিশ করে আসছিলেন। তবে এটি এনবিআর সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে, কারণ অর্থ মন্ত্রণালয় এখানে কিছু সংশোধন আনার কথা বলেছে।
১৪. ভেঙে পড়া সামষ্টিক অর্থনীতিকে জোড়া লাগানোর একটা জরুরি কাজ ছিল। এটি অন্তর্বর্তী সরকার সফলভাবেই করতে পেরেছে। তবে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা একটা বিষয় আর সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের স্বস্তি আরেকটা বিষয়। সেখানে প্রশ্ন আছে। আরেকটা বড় সূচক বলা যেতে পারে ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি। সেটি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারত। সেখানে কোনো বিপর্যয় ঘটেনি। তা সরকার কাটাতে পেরেছে। তবে রাষ্ট্রের প্রাত্যহিক শাসনের সূচক যদি আমরা দেখি, সেখানে বড় ধরনের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিচার ব্যবস্থা, দুর্নীতি ইত্যাদি আমরা দেখছি। অর্থাৎ, এখানে সরকারের সক্ষমতার ব্যাপক ঘাটতি স্পষ্ট। ঘোষণা অনেক কিছু হয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। ঘোষণা ও বাস্তবায়নের ফারাক বিস্তর।
১৫. সংস্কারের জন্য কিছু কমিশন গঠন করেছে সরকার। কিন্তু স্বৈরাচার বিলোপের গুরুত্বপূর্ণ সব অনুষঙ্গ নজরে আনা হয়নি। অতি ক্ষমতায়িত প্রধান নির্বাহী ক্ষমতা নিয়েই কেবল আলোচনা হয়েছে। যেমন– প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ কতদিন হবে ইত্যাদি। স্বৈরাচারের এটিই একমাত্র স্তম্ভ নয়। আরও চার-পাঁচটি বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত।
১৬. স্থানীয় সরকার যার সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততা অনেক বেশি, তাকে সার্বিকভাবে আরও দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। সরকার একটা কমিশন করেছে। কমিশন প্রতিবেদন দিলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। বরং স্থানীয় সরকারেও আমলাদের বসানোর প্রবণতা দেখা গেছে। এখানে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। একজন উপদেষ্টা বললেন, মসজিদ কমিটির সভাপতি পদেও নাকি প্রশাসক তথা আমলাকে বসানো হবে। এটি প্রকারান্তরে সমাজের ডায়নামিকস এবং কমিউনিটির শক্তি অস্বীকারের শামিল।
১৭. সরকারের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বড় দুর্বলতা রয়ে গেছে। রাজস্ব আদায়ে অগ্রগতি হয়নি। জিডিপির অনুপাতে রাজস্ব আয় গত অর্থবছরে আরও কমেছে। কর ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে। রাজস্ব ব্যয় বিশেষত বেতন-ভাতা, ভর্তুকি এবং ঋণের সুদ পরিশোধ এতটাই বেড়েছে যে, আমরা রাজস্ব আয়-ব্যয় উদ্বৃত্ত উন্নয়ন ব্যয়ে দিতে পারছি না। উন্নয়ন ব্যয়ের পুরোটা ঋণনির্ভর হয়ে গেছে। সরকারের আয় ও ব্যয়ের এই দুর্বলতার মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণ আগামীতে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠ মনোযোগ দরকার।
১৮. এ সরকারের আমলে অর্থনীতির স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে স্বস্তি এসেছে, কিন্তু অর্থনীতি এখনও ঘুরে দাঁড়ায়নি। এর জন্য টেকসই সংস্কার দরকার। ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষণ তখনই দেখতে পাব– যখন মূল্যস্ফীতি এমন এক পর্যায়ে নামবে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার কমাবে। এতে ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহ, পুঁজি পণ্যের আমদানি এবং জ্বালানির বাণিজ্যিক ব্যবহার বাড়বে। তখন আমরা ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি দেখব।
১৯.গত এক বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈষম্য হ্রাসের প্রত্যাশা পূরণে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি। মনে রাখতে হবে, বৈষম্যবিরোধী চেতনার মধ্য দিয়ে দেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান হয়েছে। এই অভ্যুত্থানের ফসল যদি পিছিয়ে পড়া মানুষের উপকারে না আসে, কৃষক যদি ন্যায্য মূল্য না পায় এবং শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি যদি মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম থেকে যায়, তাহলে খুবই পরিতাপের বিষয় হবে। এছাড়া বর্তমানে নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের আর্থসামাজিক বিপন্নতা বেড়েছে। মাথায় রাখতে হবে, অর্থনীতিতে যে স্থিতিশীলতার প্রশংসা আমরা করছি, তার মধ্যে একটি কালো প্রচ্ছায়া কিন্তু রয়ে গেছে। এখানে সরকারের মনোযোগ বাড়ানো খুবই জরুরি।
২০.সবশেষে বলা যায় বিগত এক বছরে অন্তর্বর্তী সরকার অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অনেক কম। অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা বজায় রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রাথমিক উৎসাহ ছিল তা ধীরে ধীরে কমে গেছে। তাদের জীবনের গুণগত পরিবর্তন হয়নি, হওয়ার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। সরকার থেকে যা বলা হয়েছিল তা বাস্তব রূপ পায়নি। অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে, যা মানুষকে আশাহত করেছে।এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব তুলে দেয়ার বিকল্প নেই। অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদেরই নিতে হবে।
লেখক: গবেষক ও অধ্যাপক

৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল গগনচুম্বী। জনগণ আশা করেছিল নতুন অন্তর্বর্তী সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করবে, অর্থনীতিকে গতিশীল করবে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাওয়া ছিল একটি গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করে মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দেও য়া এবং একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরে যাওয়া যদিও আগামী ফেব্রোয়ারীতে রমযানের আগে নিবর্চনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এক বছর পর যদিও কয়েকটা অর্থনৈতিক সূচক কিছুটা উন্নতি করেছে, অধিকাংশ সূচকই এখনো আগের দুর্বল অবস্থান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। কিছু ইতিবাচক উদ্যোগের ফলে অর্থনীতি উপকৃত হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ ছিল উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। এক বছরের ব্যবধানে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ১১ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ৮.৫৫ শতাংশে এবং খাদ্যমূল্যস্ফীতি ১৪ শতাংশ থেকে প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। তবে সাধারণ মানুষের অভিযোগ, আয়ের তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় এখনো আগের চেয়ে বেশি। এখন পর্য়ায়ক্রমে মূল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। যেমন :
১. সার্বিকভাবে বলা যায়, ব্যাংক খাতের কিছুটা উন্নতি হলেও দুর্দশা কাটেনি। তবে ব্যাংক খাত নিয়ে আগের মতো আতঙ্ক নেই । ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএফ) সাবেক নির্বাহী পরিচালক বলেন, ‘বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরকারের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয়েছে, যা ব্যাংকব্যবস্থাকে দুর্বল করে তুলেছে। এখন পরিবর্তনের আশা আছে এবং বর্তমান সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে সুশাসন ফেরানোটা জরুরি। ব্যাংক খাতে যত দ্রুত সুশাসন ফেরাতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি ব্যাংক খাত ঘুরে দাঁড়াবে।’ তিনি বলেন, ‘গত বছর গ্রাহকদের আস্থার সংকট ছিল। যেটা এখন অনেক কেটে গেছে। যদিও কিছু কিছু ব্যাংক এখনও আস্থা অর্জন করতে পারেনি। তবে কঠোর পদক্ষেপ যা নেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা গেলে ব্যাংক খাত আরও ভালো করবে।’
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি, আর আইএমএফের বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে তা ২৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান গত বুধবার রাতে এসব তথ্য জানান। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ বর্তমানে ২০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি, যা দিয়ে সাড়ে তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব।
৩. রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ স্থিতিশীল থাকায় ডলারের ওপর চাপ কমেছে। গত ১০ মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি না করায় পরিস্থিতি আরও উন্নত হয়েছে। এর পাশাপাশি বাজেট সহায়তা ও ঋণ হিসেবে কয়েক বিলিয়ন ডলার বিদেশি সহায়তাও রিজার্ভ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে আমদানি নিয়ন্ত্রিত থাকায় ডলারের চাহিদা কমে বিনিময় হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে ডলারের দাম অতিরিক্ত কমে যাওয়া রোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিলামের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ডলার কিনছে।
৪. অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর ব্যাংকগুলোয় তদারকি জোরদার করে বাংলাদেশ ব্যাংক। পাশাপাশি এতদিন নীতিমালায় যেসব ছাড় দেওয়া হয়েছিল, তা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে। এ ছাড়া আগের সরকারের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংকগুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাংক রেজুলেশন অধ্যাদেশ অনুমোদন দিয়েছে। যার অধীন ব্যাংক একীভূত, অধিগ্রহণ ও অবসায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। এজন্য সংকটে পড়া ব্যাংকগুলোর সম্পদের মান ও সুবিধাভোগী যাচাইয়ে বিদেশি নিরীক্ষক দিয়ে নিরীক্ষা চলছে। যার মাধ্যমে ৬টি ইসলামী ধারার ব্যাংককে একীভূত করার পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব ব্যাংককে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও দেশি ভালো বিনিয়োগকারী এনে শক্তিশালী করার চিন্তা চলছে।
৫. নতুন সরকার অর্থ পাচার রোধে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ায় সুফল পেয়েছে দেশের অর্থনীতি। এদিকে অর্থ পাচার রোধে সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এখন কিছুটা সক্রিয় হয়েছে। তবে ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছেন অর্থ আত্মসাতে জড়িত গ্রাহক ও ব্যাংক কর্মকর্তারা।
৬. মোট ১৪টি ব্যাংকের বোর্ড পুনর্গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। যা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে একীভূত করে একটি সুদৃঢ়, স্বচ্ছ ও সংগঠিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার অংশ। তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর জানিয়েছিলেন, দুর্বল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো একীভূত করা হবে, যাতে তাদের কার্যক্রম আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ হয়। সরকারের চলমান অর্থনৈতিক সংস্কারের অংশ হিসেবে ছয়টি নতুন আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যার মধ্যে ব্যাংক রেজুলেশন অ্যাক্ট ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ও ব্যাংক কোম্পানি অ্যাক্ট সংশোধনের কাজও চলছে।
৭. প্রবাসী বাংলাদেশিরা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেকর্ড পরিমাণ ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছে। যা দেশের ইতিহাসে এক অর্থবছরে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ। তার আগের অর্থবছর ২০২৩-২৪ রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার। যার তুলনায় রেমিট্যান্স প্রবাহ ২৬ দশমিক ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং রেমিট্যান্স আসায় গত অর্থবছরের মাস হিসেবে সর্বোচ্চ, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে। রেমিট্যান্সের সেই জোয়ার ২০২৫-২৬ অর্থবছরেও চলমান আছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দুই দশমিক ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। আগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় এটি প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি। এমনকি আগস্ট মাসের প্রথম পাঁচ দিনেও এই ধারা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, আগস্টের প্রথম পাঁচ দিনে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৮১ দশমিক ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। গত বছরের একই সময়ে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল ১৮১ মিলিয়ন ডলার।
৮. বিগত সরকারের আমলে অনিয়মের মাধ্যমে ভুয়া বা বেনামে ঋণ দেওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংক প্রয়োজনীয় ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (সিআরআর) রাখতে ব্যর্থ হলে ব্যাংকটিকে ২ হাজার ৩০৮ কোটি টাকা জরুরি ডিমান্ড লোন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মোট পরিশোধিত ঋণের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক জুনে ৮০৮ কোটি এবং ৩১ জুলাই আরও ৭০০ কোটি টাকা পরিশোধ করে। এর ফলে এখন প্রায় ৮০০ কোটি টাকার ঋণ বকেয়া রয়েছে। ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (সিআরআর) হলো একটি ব্যাংকের গ্রাহক আমানতের সেই অংশ, যা ঋণ হিসেবে বিতরণ না করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত ও শরিয়াহভিত্তিক উভয় ব্যাংককেই মোট আমানতের ৪ শতাংশ সিআরআর হিসেবে জমা রাখতে হয়।
৯. তবুও জ্বালানি সংকট ও আর্থিক খাতে জটিলতা রয়ে গেছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের কারণে বিভিন্ন প্রণোদনা বন্ধ হওয়া, উচ্চ সুদের হার এবং বিনিয়োগ হ্রাস আগামী অর্থবছরগুলোতেও প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলবে। অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ, টেকসই বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে এবং প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সরকারকে আরও মনোযোগী হতে হবে।
১০. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২৫ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ। ২০২৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৪ দশমিক ২২ শতাংশ। কম প্রবৃদ্ধির পেছনে রয়েছে বিনিয়োগের ঘাটতি, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সরবরাহ ব্যবস্থা-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, চাহিদার হ্রাস এবং সঠিক আর্থিক প্রণোদনার অভাবের মতো সমস্যা।
১১. উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সুদের হারে বিধিনিষেধ শিথিল করে বাজারভিত্তিক করা হয়েছে। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি এবং সরকারি প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছে। প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যে আমদানি শুল্ক কমিয়ে, দৈনন্দিন পণ্যের ক্ষেত্রে এলসি-বিষয়ক বাধ্যবাধকতা তুলে নিয়ে এবং খাদ্য ও সার আমদানিকারকদের জন্য ঋণের সুবিধা দিয়ে সরবরাহজনিত সমস্যা প্রশমনের চেষ্টা করা হয়েছে যাতে মূল্যস্ফীতি না বাড়ে। প্রথম দিকে তেমন ফলাফল দেখা না গেলেও মূল্যস্ফীতি এখন কমার দিকে। দীর্ঘ দুই বছরের বেশি সময় ধরে মূল্যস্ফীতি দুই অংকে থাকার পর তা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। জুলাই ২০২৪-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ, যা ২০২৫ সালের জুনে এসে ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমেছে।
১২. অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর সবচেয়ে আলোচিত দিক ছিল বিভিন্ন খাতে সংস্কার উদ্যোগ। যদিও সরাসরি অর্থনৈতিক খাতে সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়নি, পরিকল্পনা উপদেষ্টা একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল সমতা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল তৈরি করা। এই টাস্কফোর্স রিপোর্টে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যকর সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্টটি প্রধান উপদেষ্টার কাছে হস্তান্তর করা হলেও সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো স্বল্পমেয়াদে কিছু সুপারিশের বাস্তবায়নে আগ্রহ দেখায়নি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালী করতে পরিকল্পনা উপদেষ্টা আরো একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছেন যাতে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উন্নত হয়। আশা করা যায়, এখান থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।
১৩. আলোচিত আরেকটি সংস্কার হলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ( এনবিআর) পুনর্গঠন। গত ১২ মে সরকার ‘রেভিনিউ পলিসি অ্যান্ড রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট অর্ডিন্যান্স’ জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে দুটি আলাদা বিভাগে ভাগ করার ঘোষণা দেয়—‘রেভিনিউ পলিসি বিভাগ’ এবং ‘রেভিনিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ’। এটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণ কর্মসূচির একটি শর্ত ছিল। তবে কর ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির জন্য বহুদিন ধরেই অর্থনীতিবিদ ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা এ ধরনের বিভাজনের সুপারিশ করে আসছিলেন। তবে এটি এনবিআর সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে, কারণ অর্থ মন্ত্রণালয় এখানে কিছু সংশোধন আনার কথা বলেছে।
১৪. ভেঙে পড়া সামষ্টিক অর্থনীতিকে জোড়া লাগানোর একটা জরুরি কাজ ছিল। এটি অন্তর্বর্তী সরকার সফলভাবেই করতে পেরেছে। তবে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা একটা বিষয় আর সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের স্বস্তি আরেকটা বিষয়। সেখানে প্রশ্ন আছে। আরেকটা বড় সূচক বলা যেতে পারে ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি। সেটি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারত। সেখানে কোনো বিপর্যয় ঘটেনি। তা সরকার কাটাতে পেরেছে। তবে রাষ্ট্রের প্রাত্যহিক শাসনের সূচক যদি আমরা দেখি, সেখানে বড় ধরনের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিচার ব্যবস্থা, দুর্নীতি ইত্যাদি আমরা দেখছি। অর্থাৎ, এখানে সরকারের সক্ষমতার ব্যাপক ঘাটতি স্পষ্ট। ঘোষণা অনেক কিছু হয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। ঘোষণা ও বাস্তবায়নের ফারাক বিস্তর।
১৫. সংস্কারের জন্য কিছু কমিশন গঠন করেছে সরকার। কিন্তু স্বৈরাচার বিলোপের গুরুত্বপূর্ণ সব অনুষঙ্গ নজরে আনা হয়নি। অতি ক্ষমতায়িত প্রধান নির্বাহী ক্ষমতা নিয়েই কেবল আলোচনা হয়েছে। যেমন– প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ কতদিন হবে ইত্যাদি। স্বৈরাচারের এটিই একমাত্র স্তম্ভ নয়। আরও চার-পাঁচটি বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত।
১৬. স্থানীয় সরকার যার সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততা অনেক বেশি, তাকে সার্বিকভাবে আরও দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। সরকার একটা কমিশন করেছে। কমিশন প্রতিবেদন দিলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। বরং স্থানীয় সরকারেও আমলাদের বসানোর প্রবণতা দেখা গেছে। এখানে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। একজন উপদেষ্টা বললেন, মসজিদ কমিটির সভাপতি পদেও নাকি প্রশাসক তথা আমলাকে বসানো হবে। এটি প্রকারান্তরে সমাজের ডায়নামিকস এবং কমিউনিটির শক্তি অস্বীকারের শামিল।
১৭. সরকারের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বড় দুর্বলতা রয়ে গেছে। রাজস্ব আদায়ে অগ্রগতি হয়নি। জিডিপির অনুপাতে রাজস্ব আয় গত অর্থবছরে আরও কমেছে। কর ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে। রাজস্ব ব্যয় বিশেষত বেতন-ভাতা, ভর্তুকি এবং ঋণের সুদ পরিশোধ এতটাই বেড়েছে যে, আমরা রাজস্ব আয়-ব্যয় উদ্বৃত্ত উন্নয়ন ব্যয়ে দিতে পারছি না। উন্নয়ন ব্যয়ের পুরোটা ঋণনির্ভর হয়ে গেছে। সরকারের আয় ও ব্যয়ের এই দুর্বলতার মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণ আগামীতে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠ মনোযোগ দরকার।
১৮. এ সরকারের আমলে অর্থনীতির স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে স্বস্তি এসেছে, কিন্তু অর্থনীতি এখনও ঘুরে দাঁড়ায়নি। এর জন্য টেকসই সংস্কার দরকার। ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষণ তখনই দেখতে পাব– যখন মূল্যস্ফীতি এমন এক পর্যায়ে নামবে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার কমাবে। এতে ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহ, পুঁজি পণ্যের আমদানি এবং জ্বালানির বাণিজ্যিক ব্যবহার বাড়বে। তখন আমরা ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি দেখব।
১৯.গত এক বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈষম্য হ্রাসের প্রত্যাশা পূরণে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি। মনে রাখতে হবে, বৈষম্যবিরোধী চেতনার মধ্য দিয়ে দেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান হয়েছে। এই অভ্যুত্থানের ফসল যদি পিছিয়ে পড়া মানুষের উপকারে না আসে, কৃষক যদি ন্যায্য মূল্য না পায় এবং শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি যদি মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম থেকে যায়, তাহলে খুবই পরিতাপের বিষয় হবে। এছাড়া বর্তমানে নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের আর্থসামাজিক বিপন্নতা বেড়েছে। মাথায় রাখতে হবে, অর্থনীতিতে যে স্থিতিশীলতার প্রশংসা আমরা করছি, তার মধ্যে একটি কালো প্রচ্ছায়া কিন্তু রয়ে গেছে। এখানে সরকারের মনোযোগ বাড়ানো খুবই জরুরি।
২০.সবশেষে বলা যায় বিগত এক বছরে অন্তর্বর্তী সরকার অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অনেক কম। অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা বজায় রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রাথমিক উৎসাহ ছিল তা ধীরে ধীরে কমে গেছে। তাদের জীবনের গুণগত পরিবর্তন হয়নি, হওয়ার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। সরকার থেকে যা বলা হয়েছিল তা বাস্তব রূপ পায়নি। অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে, যা মানুষকে আশাহত করেছে।এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব তুলে দেয়ার বিকল্প নেই। অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদেরই নিতে হবে।
লেখক: গবেষক ও অধ্যাপক

বিএনপি, যাদের এক দশকের বেশি সময় ধরে রাজনীতিতে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল, তারা চাইছিল ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন হোক, যাতে তারা নিজেদের অবস্থান ফের শক্ত করতে পারে। তবে এনসিপি ও জামায়াত মনে করে, আগে সংবিধান সংস্কার ও নির্বাচন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দরকার—তারপরেই জাতীয় নির্বাচন দেওয়া যেতে পার
৪ দিন আগে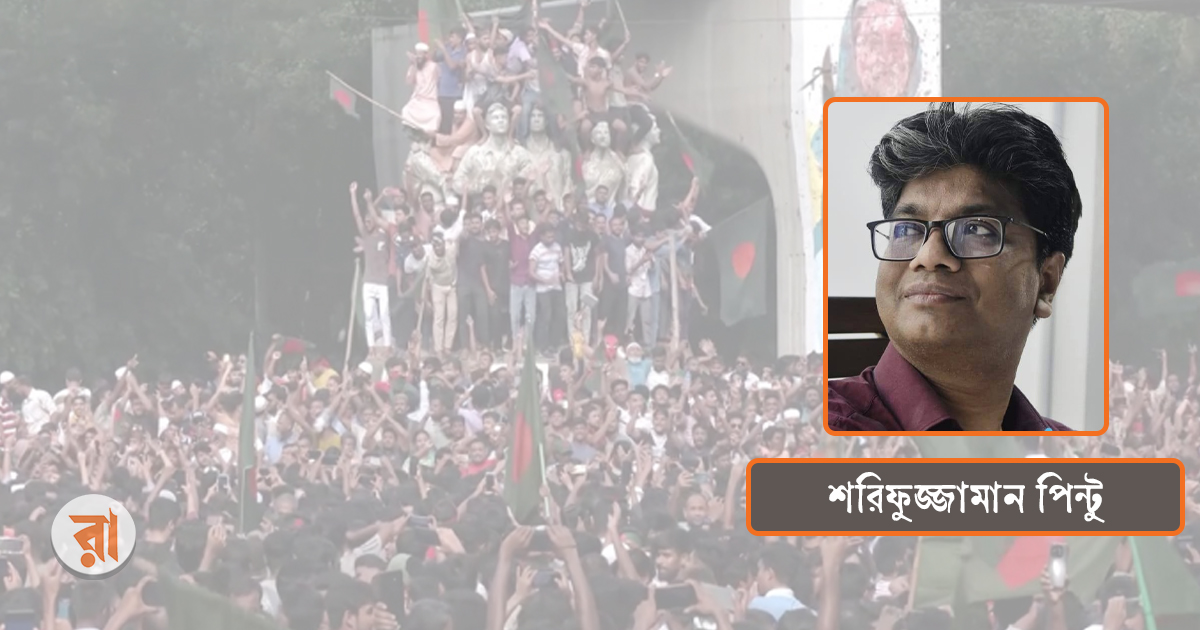
দিনটি এখন ইতিহাসে খোদাই হয়ে আছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়— এটা কি কেবল রোমাঞ্চকর এক স্মৃতি, নাকি বদলে দিয়েছে দেশের ভবিষ্যৎগতি? যে আগুন জ্বলে উঠেছিল সেদিন, তা কি এখনও দীপ্ত? নাকি ঢেকে যাচ্ছে নতুন হতাশার ছায়ায়?
৬ দিন আগে
তবে বহু বছর পর ব্যাংক ও বীমা খাত একসঙ্গে ধনাত্মক ধারায় প্রবেশ করেছে। এর কৃতিত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর দাবি করতেই পারেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে ব্যাংক খাতে নীতি ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে গেছেন এবং আমানতকারীদের আস্থা ধরে রেখেছেন।
৮ দিন আগে
আমরা যদি পেছনের দিকে ফিরে তাকাই দেখা যায় যে, যুক্তরাজ্যই মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার বালফোর ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর জায়নবাদী নেতা ব্যারণ রথচাইল্ডকে এক পত্রে বৃটিশ সরকার কর্তৃক ইহুদী জনগণের জন্য ফিলিস্তিনে জাতীয় আবাসভূমি গড়ে
৯ দিন আগে